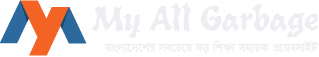↬ সৌজন্যবোধ
↬ মানবজীবনে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ
↬ জীবন গঠনে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের প্রয়োজনীয়তা
↬ ছাত্রজীবনে শিষ্টাচার ও সৌজন্য
শিষ্টাচার কি? : আচরণে ভদ্রতা ও সুরুচিবোধের যৌক্তিক মিলনের নাম শিষ্টাচার। শিষ্টাচার মনের সৌন্দর্যের বাহ্য উপস্থাপনা। তার মার্জিততম প্রকাশ ঘটে সৌন্দর্যবোধের মাধ্যমে। যে মানুষ যত বেশি শিষ্ট তার প্রিয়তাও তত বেশি। আর এই শিষ্টতা তার চরিত্রকেও করে আকর্ষণীয়। মানুষের মাঝে লালিত সুন্দরের প্রকাশ তার চরিত্র। শিষ্টতা সেই সুন্দরের প্রতিমূর্ত রূপ।
অন্তর্গত মহত্ত্ব মানুষকে উদার করে। আর সেই উদারতা ব্যক্তিকে রূঢ় করে না, তাকে শিষ্ট আর ভদ্র হতে শেখায়। মানুষের মাঝে এই মহত্ত্বের পরিশীলিত প্রকাশই শিষ্টতা। সাধারণভাবে চালচলন, কথাবার্তায় যে ভদ্রতা, শালীনতা আর সৌজন্যের পরিচয় পাওয়া যায় তা-ই শিষ্টতা। শিষ্টাচার ব্যক্তিজীবনের যেমন তেমনি সমাজজীবনেরও গৌরবসূচক আভরণ।
আচরণে যদি মানুষ শিষ্ট না হয়, ব্যবহারে উগ্রতা যদি পরিহার না করে তবে কখনো শিষ্টাচার হওয়া সম্ভব নয়। স্বভাবে কৃত্রিমতা পরিহার করতে না পালে কখনো পবিত্র মনের অধিকারী হওয়া যায় না। মানবিক সত্তা তার স্ফুরণে চরিত্রে সাধুতাকে অবলম্বন করে, তার প্রকাশ ঘটে শিষ্ট স্বভাবে। ঐদ্ধত্য আর উচ্ছৃঙ্খলতা এখানে পরাজিত হয়। অহংকার অন্যকে ছোট ভাবতে শেখায়। শিষ্টতা বিপরীতভাবে মানুষকে সম্মান করতে শেখায়। কদর্যতা আর অশ্লীলতা শিষ্টাচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। কাজেই ব্যক্তিকে হতে হয় আচরণে মার্জিত, বক্তব্যে সৎ, সরল আর স্পষ্ট। বিনয় মানুষকে ছোট করে না, বরং পরায় সম্মানের মুকুট। এই বিনয় শিষ্টতার অঙ্গভূষণ।
শিষ্টাচারের গুরুত্ব : আচরণে যে জাতি যত বেশি সভ্য সে জাতি তত বেশি সুশৃঙ্খল ও উন্নত। কেবল পশুপাখির মতো বেড়ে ওঠাই মানুষের লক্ষ্য নয়। আত্মোন্নয়নের পাশাপাশি সমাজ ও জাতীয় জীবনে কোনো-না-কোনো ভাবে অবদান রাখা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। আর তা করতে হলে শিষ্ট আচরণের অনুশীলন ছাড়া বিকল্প নেই। শিষ্টাচারের প্রথম প্রকাশ ঘটে ব্যক্তিস্বভাবে। যা ক্রমাগত ব্যক্তি থেকে আলোর বন্যার মতো ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজে, রাষ্ট্রে। এর আলোতে উজ্জ্বল ব্যক্তির আত্মিক মুক্তির সাথে যোগ হয় বৈষয়িক অগ্রগতি। সমাজবদ্ধ জীব হিসেবে প্রতিনিয়তই আমাদের সমাজের অপরাপর দশ জনের সাথে যোগাযোগ আর ভাবের আদান-প্রদান করতে হয়। এরই মাঝে শিষ্টজন সহজে সকলের মন জয় করতে পারে। পারস্পরিক সম্প্রীতির জন্যে এর খুবই প্রয়োজন। কেননা সম্প্রীতি না থাকলে হিংসা আর হানাহানি সমাজকে ঠেলে দেয় বিশৃঙ্খলার দিকে।
শিষ্টাচারী ব্যক্তি দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার সৌজন্যে আর বিনয়ের মাধ্যমে সে সকলের প্রিয়তা অর্জন করে। শিষ্টজন সহজেই অর্জন করেন অন্যের আস্থা। অন্যের সহানুভূতি লাভ করার জন্যে শিষ্টজনই উত্তম। অপর দিকে শিষ্টাচারীকে সকলে সম্মানের চোখে দেখে। সামাজিক সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্যে শিষ্টাচারের বিকল্প নেই। এতে করে আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সকলের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে আসে সুষম উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি।
শিষ্টাচার ও ছাত্রসমাজ : জ্ঞানার্জনে নিষ্টা, অভিনিবেশ আর শৃঙ্খলাবোধের পাশাপাশি শিষ্টাচার অনুশীলন খুবই জরুরি। নৈতিক চরিত্রে উৎকর্ষের জন্যে ছাত্রজীবনেই ব্যবহারের ভব্যতা আর শিষ্টতার সম্মিলন ঘটানোর কোনো বিলল্প নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে জ্ঞানের সাথে শিষ্টাচারের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। ছাত্রজীবনে শিষ্টাচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ ঘটে পোশাক-পরিচ্ছদে। রুচিশীল আর সরল জীবন-যাপনের পাশাপাশি পোশাকের ক্ষেত্রেও সুরুচির পরিচয় থাকা দরকার।
শিষ্টাচার ও সমাজ : সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক- প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তা না হলে বিদ্বেষ, হিংসা, হানাহানি আর অশান্তি জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। শিষ্টাচার প্রতিষ্ঠায় সমাজ-ব্যবস্থা ও সমাজ কাঠামোর প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাব প্রদর্শন করা দরকার। কিন্তু তার মানে এই নয় যে যৌক্তিক সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনকে এগিয়ে নিলে শিষ্টাচারী হওয়া যাবে না। সমাজে নিজের অবস্থান সম্পর্কে থাকতে হবে সতর্ক। সামাজিক অবস্থান শিষ্টাচারের মাত্রা নির্ধারণ করে। এই ভাবে ক্রোধ আর প্রতিহিংসার মতো চারিত্রিক দোষগুলো অতিক্রমের চেষ্টা থাকতেই হবে। এব বিপরীতমখী দিনগুলো নিয়ন্ত্রণের জন্যে দরকার চারিত্রিক দৃঢ়তা।
শিষ্টচার ও রাষ্ট্র : জাতীয় জীবনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে শিষ্টতার প্রকাশ পায় রাষ্ট্র পরিচালনায়, নেতৃত্ব প্রদানকারীদের মধ্যে। এর প্রভাব পড়ে গোটা দেশজুড়ে। আবার আন্তঃরাষ্ট্র সম্পর্ক বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণে কুটনৈতিক কর্মকাণ্ডে শিষ্টতার বিকল্প নেই। চরম লাভ-লোকসানের ব্যাপার ব্যবসা-বাণিজ্যেও শিষ্টচারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
শিষ্টাচার না থাকার কুফল : শিষ্টাচারহীন সমাজ ও অন্তঃসারশূন্য, বিবেকহীন। সমাজে সৌন্দর্য আর সুকুমার প্রবৃত্তিগুলোর দেখা মেলে না। মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে বিরোধ হয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়। সর্বোপরি মানব সভ্যতা চরম হুমকির মুখোমুখি দাঁড়ায়। শিষ্টাচারহীন মানুষ সবসময় উদ্ধত থাকে। আলাপ-আলোচনায় তার মধ্যে প্রকাশ পায় অমার্জিত ভাব। তার আচরণে প্রাধান্য পায় দুর্ব্যবহার ও দুর্মুখতা।
শিষ্টাচার অর্জনের উপায় : শিষ্টাচার নিজ থেকে মানব হৃদয়ে জন্ম নেয় না। একে বরণ করে নিতে হয়। এর চর্চা শুরু হয় শিশুকাল থেকেই। তাই শিশু কোন পরিবেশে, কার সহচর্যে কীভাবে বেড়ে উঠছে সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে পয়োজন শিক্ষার। কেননা আমৃত্যু চলতে থাকে শিষ্টাচারের অনুশীলন। শিশু পরিবার-পরিজন, সঙ্গী-সাথী কিংবা প্রতিবেশী যাদের সাহচর্য়ে থাকে তাদের কাছ থেকেই আচরণ শেখে। তাই সৎসঙ্গ শিষ্টাচারী হতে সাহায্য করে। স্কুল-কলেজেও শিক্ষার্থীরা শিষ্টাচারের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। ভালো বইও একজন সৎ অভিবাবকের মতোই শিষ্টাচার শেখাতে পারে।
উপসংহার : শিষ্টাচারের ভিত্তিভূমিকার ওপর গড়ে ওঠে সৎ চরিত্রের সুরম্য অট্টালিকা। সৎ চরিত্রবান ব্যক্তি সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা শিষ্টাচারের অন্তরায়। তা প্রতিনিয়ত মানবিক মূল্যবোধগুলো ধ্বংস করে সমাজকে করে তুলতে পারে নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্বান্ত। মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়ে আমরা হতে পারি সমস্যা-জর্জরিত। এ থেকে পরিত্রাণ পেতে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনে সুস্থতা ও সমৃদ্ধি অর্জনে তাই আমাদের শিষ্টাচারের চর্চা করা উচিত।
[ একই প্রবন্ধ আরেকটি বই থেকে সংগ্রহ করে দেয়া হলো ]
ভূমিকা : সুন্দর আচরণ ও ব্যবহারই হল শিষ্টাচার। সে আচরণ- কথাবার্তায়, কাজকর্মে, চলনে-বলনে, রীতিনীতিতে সর্বোপরি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। যাকে বলে আদব-কায়দা মেনে চলা বা ভদ্র ব্যবহার ও সৌজন্যবোধ দেখানো; তাই মূলত শিষ্টাচার। সত্যিকারের মানুষের পরিচয় তার সুন্দর, সংযত ও বিনয়ী ব্যবহারে। রাজা সলোমন বলেছেন,
‘অহঙ্কার মানুষের পতন ঘটায়, কিন্তু বিনয় মানুষের মাথায় সম্মানের মুকুট পরায়।’
শিষ্টাচার হল এই বিনয় বা নম্রতা, বিশেষ করে আচরণে তার সার্থক বহিঃপ্রকাশ। দেহের সৌন্দর্য অলঙ্কার কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। অলঙ্কার বাইরের সামগ্রী আর শিষ্টাচার অন্তরের এবং সৌজন্যবোধ হল তার মার্জিততম প্রকাশ। মানুষ যতদিন অরণ্যচারী ছিল, ততদিন সে শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ প্রকাশের প্রয়োজনবোধ করে নি। যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হল, তখন থেকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের প্রয়োজন অনুভূত হলো। শিষ্টাচার সমাজ-সরসীর বিকশিত শুভ্র-সমুজ্জ্বল শতদল। শুধু আমাদের ব্যক্তিজীবনের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের সমাজজীবনেও গৌরবজনক আভরণ। Oscar Wilde তাঁর ‘The Importance of Being Earnest’ নাটকে বলেছেন,
‘Courtesy and politeness are the basic principles which directs human life smoothly.’
শিষ্টাচার ও সৌজন্য বলতে কী বোঝায় : আভিধানিক অর্থে রুচিপূর্ণ ভদ্র ব্যবহারই শিষ্টাচার-সৌজন্য। শিষ্টাচার কথাটির মধ্যেই তার তাৎপর্য লুক্কায়িত। শিষ্টাচার শব্দটিকে ভাঙলে যে দুটি শব্দ পাওয়া যায় তা হল। শিষ্ট+আচার; এর অর্থ বিনীত, সংযত, শোভন আচার-ব্যবহার। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পরিচিত-অপরিচিত সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ, রুচিসম্মত ব্যবহারই শিষ্টাচার। শিষ্টাচার ও সৌজন্য উভয়ই সমার্থক হলেও দুয়ের মধ্যে রয়েছে সূক্ষ্ম পার্থক্য। শিষ্টাচারে সকলেই মুদ্ধ হয়। আর সৌজন্য বলতে বাইরের মার্জিত ব্যবহারই শুধু নয়, নয় ভদ্রতার সামাজিক রীতি অনুসরণ, এর সঙ্গে যুক্ত আছে সুজনের মহৎ হৃদয়ের গভীর উষ্ণ স্পর্শ। আছে অন্তর- সৌন্দর্যের বিকশিত মহিমা।
মানবজীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব : দেহের সৌন্দর্য অলঙ্কার কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। অলঙ্কার বাইরের সামগ্রী আর শিষ্টাচার অন্তরের। মানুষ যতদিন অরণ্যচারী ছিল, ততদিন সে শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ প্রকাশের প্রয়োজনবোধ করে নি। যখন থেকে মানুষ সমাজবদ্ধ হল, তখন থেকে শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের প্রয়োজন অনুভূত হল। শিষ্টাচার শুধু আমাদের ব্যক্তিজীবনের সৌন্দর্যই নয়, আমাদের সমাজজীবনেরও গৌরবজনক আভরণ। শিষ্টাচারের গুণেই মানুষের সঙ্গে মানুষের যে-কোনো সম্পর্ক রাখা সম্ভবপর হয়। বড় ও বয়স্কদের সম্মান করা, সকলকে আচরণে তুষ্ট করা, ঔদ্ধত্যকে পরিহার করা এবং সবার সঙ্গে প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলাই তো মানবিক বৈশিষ্ট্য। মার্জিত রুচি ও সুন্দর মনের পরিচয় দিতে হলে কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে আমাদের হওয়া উচিত নম্র ও বিনয়ী। শিষ্টাচার ও সৌজন্য সামাজিক মানুষের এক দুর্লভ ঐশ্বর্য। একে আয়ত্ত করেই মানুষের গর্ব, তার অহঙ্কার, তার গৌরব। যে-মানুষ এই সম্পদের অধিকারী, সে-মানুষই তত ভদ্র ও বিনয়ী। যে সমাজ একে সাদরে গ্রহণ করেছে, সে-সমাজই সে-পরিমাণে সভ্য। তার লোক-ব্যবহারও তত মার্জিত, সদ্ভাবমূলক। একে নর্বাসন দিয়ে মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়। উন্নত সভ্যতা তো এরই অবদানপুষ্ট। এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য কোনো অর্থ বা ঐশ্বর্য দিয়েই কেনা যায় না।
ছাত্রজীবনে শিষ্টাচারের গুরুত্ব : ছাত্রজীবন হল মানুষের প্রস্তুতিপর্ব। এরই ওপর নির্ভর করে তার পরবর্তী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। নির্ভর করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-প্রকৃতি। এসময়ই হল তার শিষ্টাচার ও সৌজন্য শিক্ষার যথার্থ কাল। তার উন্মেষ-লগ্ন। শিষ্টাচার ও সৌজন্যের ছোঁয়াতেই ছাত্র হয় বিনীত, ভদ্র। নতুন প্রাণ-সম্পদ হল গৌরবান্বিত। ছাত্রজীবনে যে গুরুজনদের শ্রদ্ধা করতে শিখল না, তার উদ্ধত, অবনীত ব্যবহারে শিক্ষক বিরক্ত, যার রূঢ়, অমার্জিত আচরণে সহ-বন্ধুরা ক্ষুব্ধ, বেদনাহত, পরবর্তী জীবনেও তার একই আচরণের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তখন সে হয় অশুভ-শক্তি, অকল্যাণের মূর্ত প্রতীক। হতাশা, ব্যর্থতার তিল তিল দংশন-জ্বালায় সে নিজেকে নিঃশেষ করে। ছাত্রজীবনই মানুষের সুকুমারবৃত্তি লালনের শুভক্ষণ। এখানেই তা চরিত্রগঠনের ব্রত-অনুষ্ঠান। শিষ্টাচার ও সৌজন্য তো তার মনুষ্যত্ব অর্জনেরই সোপান। এরই মধ্যে আছে নিজেকে সুন্দর ও সার্থকতায় পরিপূর্ণ করে তোলার মহাশক্তি। শিষ্টাচার, সৌজন্য প্রকাশের জন্যে ছাত্রদের কিছু হারাতে হয় না, কোনো অর্থ ব্যয় করতে হয় না, বরং এক মহৎ অঙ্গীকারে তার সমৃদ্ধ জীবন-বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিনয়ী, ভদ্র ছাত্র শুধু শিক্ষকের স্নেহই কেড়ে নেয় না, সে পায় শিক্ষকের আশীর্বাদ, পায় তাঁর সাহায্য। শিষ্টাচার ও সৌজন্যের অভাব ছাত্রকে অবিনীত, স্বার্থপর, নিষ্ঠুর করে। ধ্বংস করে তার প্রেম, মমতা, সহানুভূতি, দয়া ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তি। এই অভাবই তাকে ঠেলে দেয় অন্যায় ও অসত্যের চোরা-অন্ধকারে। সেই অন্ধকার শুধু ব্যক্তিকেই আচ্ছন্ন করে না, গ্রাস করে গোটা সমাজকে।
সামাজিক রীতি ও শিষ্টাচার : বিংশ শতাব্দীর অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে আমাদের একবার হিসাব-নিকাশ করতে হবে। তা’হলে দেখতে পাব, সভ্যতা আমাদের শিষ্টাচার উপহার দিয়েছে এবং তা মানুষের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। কেবল এর জন্যেই আমরা সুসভ্য মানুষ হিসেবে গর্ববোধ করতে পারি। যে সমাজ যত সভ্য, তার লোক-ব্যবহার তত মার্জিত, সদ্ভাবমূলক এবং সুরুচিব্যঞ্জক। সেই লোক-ব্যবহারকে কোথাও কোথাও রীতিমাত্র বলে ভ্রম হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে সৌভ্রাতৃত্ব ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থে কতকগুলো নিয়ম অনুসরণ করতে হয়, তাকে রীতি বলা হয়। কিন্তু ভদ্রতা রীতিমাত্র নয় রীতি কেবল বাইরের অভ্যাসমাত্র, যাতে অন্তরের স্পর্শ থাকে না।
আজ সমাজের নানা ক্ষেত্রেই অশিষ্টাচার ও সৌজন্যহীনতার নিষ্ঠুর চিত্র। দিন দিনই মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়ছে। বাড়ছে তার সীমাহীন ঔদ্ধতা। আজ বার্ধক্যকে সম্মান করি না। শ্রদ্ধেয়দের করি অবজ্ঞা, পুরাতনের প্রতি অশ্রদ্ধা। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে মানুষে মানুষে বিরোধ। চারদিকে আজ বিত্তবানের নির্লজ্জ ঔদ্ধত্য, প্রবলের সীমাহীন অত্যাচার। আজ শিষ্টাচার ও সৌজন্য দুর্বলের ভীরুতারই অসহায় প্রকাশ যেন। মানুষকে অপমান করতে পারলেই বুঝি তৃপ্তি। অবিনয় আজ আর তার লজ্জা নয়। শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের সৌন্দর্য হারিয়ে মানুষ আজ নিঃশ্ব, হৃদয়হীন। অন্তরের পুষ্পিত শতদল আজ ছিন্নভিন্ন।
শিষ্টাচার ও স্পষ্টবাদিতা বা শিষ্টাচার অর্জনের উপায় :
‘The greatest ornament of an illustrious life is modesty and humanity.’
আশৈশব আত্মসংযম ও মার্জিত প্রকাশভঙ্গির অনুশীলন-ফল হলো শিষ্টাচার। কাজেই আত্যন্তিক স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে রয়েছে শিষ্টাচারের মৌলিক গরমিল। স্পষ্টবাদিতার দোহাই দিয়ে ইতরতা বা রূঢ়তার অস্ত্র-প্রয়োগ সামাজিক শালীনতাবোধকে পীড়িত করে। তথাকথিত স্পষ্টবাদীর দল লোক-সমক্ষে নিজেদের অসাধারণরূপে জাহির করবার ঘৃণ্য লোভ সংবরণ করতে না পেরে সামাজিক শিষ্টাচারকে পদদলিত করে এক-একসময় অত্যন্ত রূঢ় কথা বলে ফেলেন। অথচ সেই সত্য বাক্যটিকে অপ্রিয়ভাবে না বলে মার্জিত ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে পারলে আত্মিক সমুন্নতি প্রকাশ পেত। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে-
‘Courtest cost nothing but buys everything.’
শিষ্টাচারের গুণে মানুষের হৃদয়ে অতি সহজেই জায়গা করে নেয়া যায়।
শিষ্টাচার ও খোশামোদ-বৃত্তি : ভদ্রতা হল সব মানুষের প্রতি সমান দৃষ্টি, আর খোশামুদির দৃষ্টি কেবল নিজের প্রতি নিবদ্ধ। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ নিজের অসুবিধা করে পরের সুবিধা করে দিতে উৎসুক; খোশামোদ-বৃত্তি বোঝে শুধু নিজের সুবিধা আর খোঁজে আত্মসুখ ও আত্মসমৃদ্ধি। শিষ্টাচার বা সৌজন্যবোধ সৌষ্ঠবমণ্ডিত, সরল ও সুন্দর। খোশামোদ-বৃত্তি সৌষ্ঠবহীন, কুটিল ও কুৎসিত। শিষ্টাচারে আছে বিশ্বমুখিনতা, আর খোশামোদ-বৃত্তিতে আছে আত্মমুখিনতা।
চক্ষুলজ্জা ও শিষ্টাচার : চক্ষুলজ্জা নামে একটি সামাজিক উপসর্গ শিষ্টাচারের বেনামীতে লোক-সমাজে প্রচলিত আছে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে অসত্যকে সত্য বলে স্বীকার করা একটি গুরুতর সামাজিক ব্যাধি। শিষ্টাচারের সঙ্গে দৃঢ়তার মিশ্রণই এই ব্যাধির সঠিক চিকিৎসা। এদেশে অসায়িক এবং লোকপ্রিয় মানুষের খুবই অভাব। তাই আমাদের সমাজে এখনো শিষ্টাচার নামক স্বভাবটি গড়ে উঠতে পারে নি।
উপসংহার : মোট কথা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় সংসার-চক্রের অনিবার্য ঘর্ষণে যে শ্বাসরোধকারী ধূম্রজাল উত্থিত হতে থাকে, শিষ্টাচারের স্নিগ্ধ শান্তি-বারি সিঞ্চনেই তা নিবারিত হতে পারে। শিষ্টাচার ধূলি-ম্লান পৃথিবীর রুক্ষতাকে কোমলতা দান করে দৈনিক জীবনযাত্রাকে শোভামণ্ডিত করে তোলে। অতিসাম্প্রতিককালের মতো মানবসভ্যতার এমন সংকট আর কখনো দেয়া যায় নি। বর্তমান শতাব্দীর অপরাহ্নে এসে সভ্যতা একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেছে। সভ্যতার যা আত্মিক সম্পদ, যা যুগ-যুগান্তরের চিৎ-প্রকর্ষের অনবদ্য যোগফল, যা কর্ম ও বাক্যের নিকষিত হেম’, সেই শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধের দুর্ভিক্ষ আজ দিকে দিকে মরু-রসনা বিস্তার করছে।